প্রাচীন ভারতের ‘ সভা ও সমিতি’ ও অধুনা রাজনৈতিক দলের সাদৃশ্য ও গুরুত্ব একটি পর্যালোচনা. ……
অর্পণ বন্দ্যোপাধ্যায় :ঊনিশ শতকের প্রথম থেকে ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে একের পর এক আদিবাসী ও কৃষক আন্দোলন এবং মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হতে থাকে । ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রসার ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর দ্রুত ঘটতে থাকে । উনবিংশ শতকে ব্রিটিশদের উদ্যোগে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটে এবং ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে । মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় উপলব্ধি করে যে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা সম্ভব নয় । এর একমাত্র উপায় হল ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন করা । ব্রিটিশদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার ।
এই উদ্দেশ্য ঊনিশ শতকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা সভাসমিতি গড়ে উঠতে থাকে । এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—(i) বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, (ii) জমিদার সভা, (iii) ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, (iv) হিন্দু মেলা, (v) ভারতসভা, (vi) জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি । এই সমস্ত রাজনৈতিক সভাসমিতি ও সংগঠন ব্রিটিশ-বিরোধী জনমত গঠনে সহায়ক হয়ে ওঠতে থাকে । এই জন্য কেমব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ড. অনিল শীল ঊনিশ শতককে ‘সভাসমিতির যুগ’ বলে অভিহিত করেছেন ।
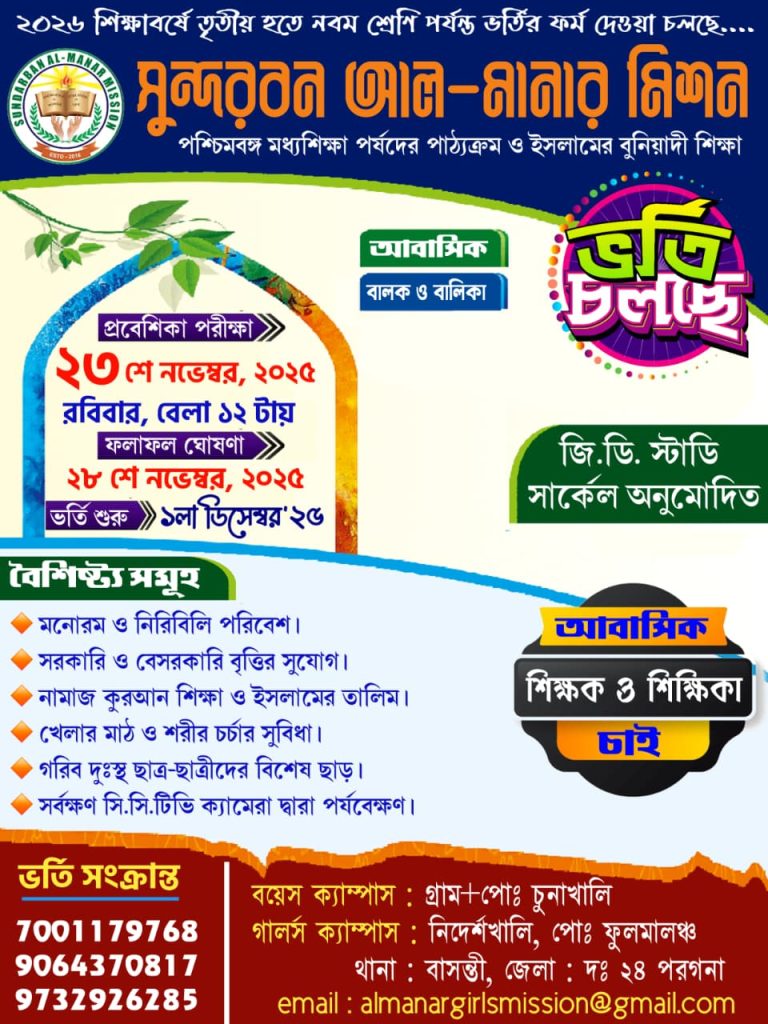
ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ভারতীয়রা সংঘবদ্ধ ছিল না । ভারতীয় শাসকশ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের পথ সুগম করেছিল । সংকীর্ণ স্বার্থে মারাঠা, শিখ সবাই মারামারি, ঝগড়া-বিবাদ করেছে । সাধারণ মানুষ রাজনীতিতে তখন কোন ভূমিকা গ্রহণ করত না । উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ প্রশাসন ভারতের রাজশাসনের অবলুপ্তি ঘটিয়ে দেশীয় রাজা ও নবাবদের কার্যত নিজেদের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসেন ।
এই সময় ভারতীয় সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে এবং দুটি বিশিষ্ট শ্রেণির মানুষের উদ্ভব হয় । প্রথমত, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় চিরস্থায়ী জমিদারি ব্যবস্থার প্রবর্তনের হলে এক নতুন ধরনের ভূস্বামী সম্প্রদায়ের জন্ম হয় । এই ধরণের জমিদাররা প্রথমদিকে তাদের জমি হারায়, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যাতে জমিদারদের আয় বাড়ে, সেদিকে নজর দিলে কৃষকশ্রেণি সরকারের ওপর অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয় । পরের দিকে আবার যখন ব্রিটিশ সরকার কৃষকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করলেন, তখন জমিদাররা সরকারের ওপর অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয় । দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটল, যারা চাকরি করার পাশাপাশি আইনব্যবসা, সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা, চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন গঠনমূলক পেশায় নিযুক্ত হল ।
এই দুই শ্রেণির মানুষ ব্রিটিশ শাসনে অসন্তুষ্ট ছিলেন । তারা তাদের চিন্তাভাবনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের পথ খোঁজার চেষ্টা করছিলেন । ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোয় ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ না থাকায় ভারতীয়রা নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলার দিকে নজর দেয় । এই ভাবেই শুরু হয় সভাসমিতির যুগ । জমিদার শ্রেণি মহাবিদ্রোহের বেশ কিছুটা আগে থেকেই তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলেছিল । মহাবিদ্রোহের পরবর্তী প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সক্রিয় প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল । এই সময়ে ভারতের বাইরেও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে । এইসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই ভারতের জনমত গড়ে উঠতে থাকে । সভাসমিতিগুলি প্রধানত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংগঠন হওয়ায় এবং সমাজের ওপরতলার মানুষেরা এইসব সভাসমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় তারা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের দাবিদাওয়া তুলে ধরেছিল । সাধারণ দরিদ্র শ্রমিক-কৃষকশ্রেণির সঙ্গে তাদের তেমন সম্পর্ক ছিল না । ফলে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবিদাওয়া এইসব সভাসমিতির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়নি । অবশ্য এইসব সভাসমিতিগুলি জাতি ও ধর্মের সংকীর্ণ সীমারেখা অতিক্রম করে গড়ে উঠেছিল এবং কলকাতা, বোম্বাই (মুম্বাই), মাদ্রাজ (চেন্নাই) পুনা (পুনে) প্রভৃতি বড় বড় শহরকে কেন্দ্র করে এইসব সভাসমিতি গড়ে ওঠে । শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলনের মধ্যে যে এক অবাস্তব আবেগধর্মী দিক ছিল তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জীবনস্মৃতি’ থেকে জানা যায় ।
ভারতে রাজনৈতিক চেতনার জাগরনে সভা সমিতি যুগের গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম -উনিশ শতকের সভা সমিতির অনুশীলনের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষ বিশ শতকের আধুনিক রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করে।
সভা সমিতি গুলি প্রকাশ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য জানালেও, তারা সরকারের কাজকর্ম ও নীতির অবিরাম ও যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করে দেশে রাজনৈতিক চেতনার জাগরন ঘটায়।
ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ঐক্য ও ইংরেজি ভাষার প্রসারের সুযোগ নিয়ে প্রাদেশিক সভা সমিতি গুলি একে অন্যের মত ও আদর্শের আদান প্রদান করে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ঘটায়।
সভা সমিতি যুগের অভিজ্ঞতা থেকে ভারতীয়রা ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতীয়দের ন্যায্য দাবি ও অধিকার গুলি আদায়ের জন্য সর্বভারতীয় সংগঠন ও সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার শিক্ষা লাভ করে।
এই শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে ভারতীয়দের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে। এরই ফলশ্রুতিতে ভারতে ১৮৮৫ খ্রিঃ সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গড়ে ওঠে। এই জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বেই ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবল আকার ধারন করে।
এইভাবেই দেখা যায়, সভা সমিতি যুগ ভারতে রাজনৈতিক চেতনার জাগরন ও প্রসারে এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনমত মানে জনগণের মতামত। জনমত গঠনে যেসব মাধ্যম ভূমিকা রাখে তার মধ্যে রাজনৈতিক দল অন্যতম। রাজনৈতিক দল সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, সভা-সমিতি, আলাপ-আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচি নিয়ে জনগণের নিকট হাজির হয়ে জনমত গঠনে সচেষ্ট থাকে। সরকার ও বিরোধী দল তাদের স্ব স্ব কর্মসূচির পক্ষে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দল জনগণকে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনুপ্রেরণা যোগায়।
লেখক: ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ব্রিলিয়ান্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল




